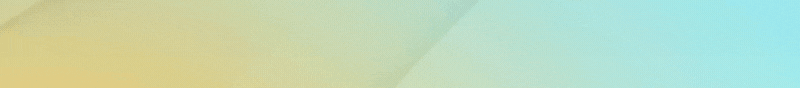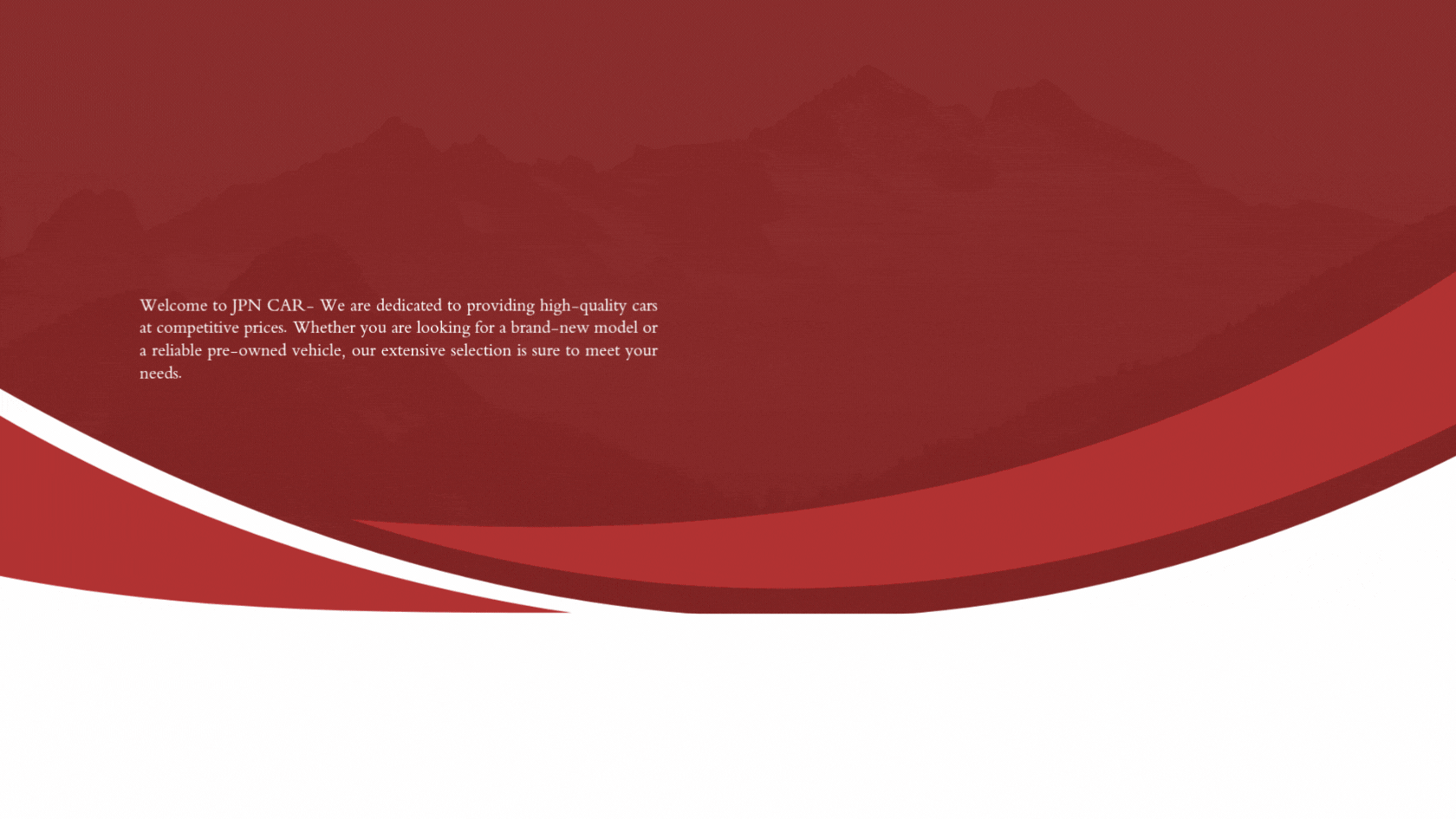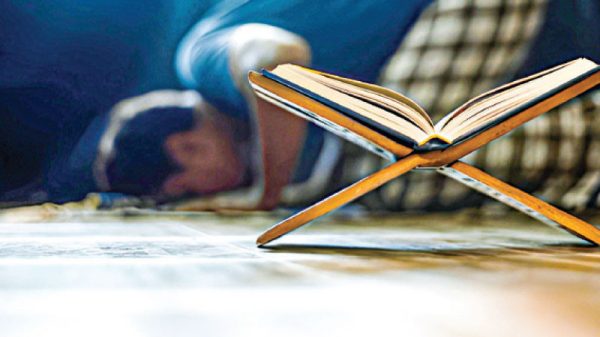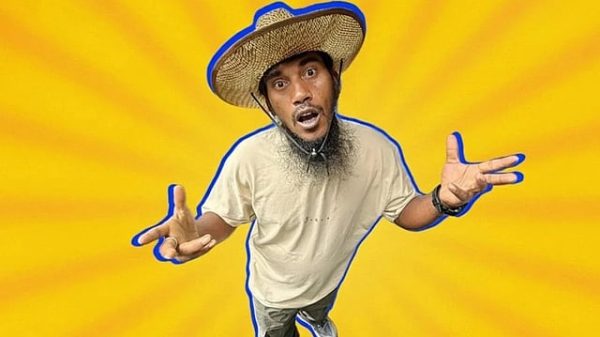বাংলাদেশের প্রযুক্তির ছোঁয়া পোশাক রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা
- প্রকাশিত: সোমবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫
- ৬১ বার পড়া হয়েছে

সম্পাদকীয় কলাম।
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের ইতিহাস প্রায় অর্ধশতক। নানা সংকটের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা পোশাক খাত এখন ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির দিকে যাচ্ছে। সরাসরি ৪০ লাখ ব্যক্তির কর্মসংস্থান দেখা গেলেও আদতে দুই কোটি মানুষ পরোক্ষভাবে এ খাতে সম্পৃক্ত। রপ্তানি আয়ের ৮০ ভাগের বেশি আসে আমাদের পোশাক খাত থেকে। এখনো বেশির ভাগ উদ্যোক্তা প্রচলিত পদ্ধতিতেই উৎপাদন করছেন। প্রবর্তিত রপ্তানি প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন ব্যবস্থা বদলে যেতে শুরু করেছে পুরো বিশ্বে। শুরু হয়েছে অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পর্ব। অটোমেশনের যাত্রার সূচনা বাংলাদেশেও হয়েছে। প্রযুক্তির এই ছোঁয়া অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
আমাদেরও অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে যেতে হবে। এতে সার্বিকভাবে রপ্তানির কাঠামোই বদলে যাবে, বের হবে নতুন সম্ভাবনা। কাজে গতি আনার পাশাপাশি প্রক্রিয়াগুলো তদারকি আরও সহজ হবে। অনেকে নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এদিকে বিনিয়োগ শুরু করেছেন। কেউ কেউ মনে করছেন, এতে কর্মসংস্থান কমে যাবে। তবে এর প্রভাব পড়বে যৎসামান্য। নতুন নতুন খাত যুক্ত হওয়ায় সেখানেই দক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান তৈরি হবে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পোশাক খাতে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না। শুধু ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনায় কিছুটা বৈচিত্র্য আসতে পারে। কিন্তু মূল বিষয়টি হল অটোমেশন। উৎপাদন পর্যায়ে অটোমেশন শুরু হলেও তা কর্মসংস্থানে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না। অনেকে মনে করছেন, অটোমেশন হলে কর্মসংস্থান কমে যাবে। আসলে উৎপাদন পর্যায়ে খুব একটা প্রভাব পড়বে না। যে পরিবর্তনটা বেশি হবে, তা হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের পরবর্তী অবস্থায়—রপ্তানি কার্যক্রমে। সেখানে গতি আসবে।কাপড়ের সেরা দোকান
এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো আসবে। বর্তমানে নকশা এবং ডকুমেন্টেশনের মত কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় পণ্য পরিবহন, লোড, আনলোড ও প্যাকেজিং প্রক্রিয়ায় আরও সময় বাঁচবে, কাজ হবে দ্রুততর। পণ্যের অর্ডার থেকে শুরু করে রপ্তানি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে দেখা ও বুঝতে পারা যাবে—মানে হল, উৎপাদনের কোন কাজ কোন পর্যায়ে আছে, তা দেখা যাবে। এতে পুরো প্রক্রিয়াটা একটিমাত্র ব্যবস্থাপনার মধ্যে চলে আসবে।
তখন আমাদের সময় বাঁচবে। পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়বে। এ জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশন—দুটোই দরকার। হয়তো একসময় পুরো অটোমেশনে না থাকা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অটোমেশন থাকা কোম্পানি বেশি অর্ডার পাবে। কারণ, বায়াররা তো সব জানতে চাইবে। এ জন্য অটোমেশনে যেতেই হবে। তাই যে বিনিয়োগ লাগবে, তা হয়তো সবাই করতে পারবে না। আমরা বিজিএমইএর জন্য তিন শ্রেণিতে ভাগ করি প্রতিষ্ঠানগুলোকে। বৃহৎ ও মধ্যম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো এ খাতে নতুন বিনিয়োগ করার সক্ষমতা রাখে।
সবচেয়ে সংকটে পড়বে এসএমই প্রতিষ্ঠান। ছোট ছোট অর্ডার তারাই করে। অনেক সময় দেখা যায়, বড় বায়ারের ছোট অর্ডার এসেছে, তখন তা অন্য প্রতিষ্ঠান দিয়ে করিয়ে দিতে হয়। এসব ছোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। কর্মসংস্থানেও তারা অবদান রাখছে। বিজিএমইএ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে। এটি করে যাবে। সরকার যদি চায়, কর্মসংস্থানে জড়িত এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকুক এবং কর্মসংস্থান বাড়ুক, তাহলে বিশেষ সুদে ঋণ দিতে পারে। নয়তো নতুন ধাক্কা সামলাতে পারবে না তারা।
২.
শ্রমিক অসন্তোষ মাঝেমধ্যেই একটা বিরূপ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় পুরো খাতকে। মূলত কিছু নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক—উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান আইন মেনে চলার মানসিকতা না থাকার কারণে এটি হচ্ছে। আইন তো মানতে হবে, সেটা শ্রম আইন হোক বা আন্তর্জাতিক কোনো চর্চা হোক। আমাদের মধ্যে আইন মানার মানসিকতা এখনো গড়ে উঠছে না। এটি না করায় উদ্যোক্তার ব্যবসা টেকসই হয় না। পটপরিবর্তন বা রাজনৈতিক সরকারের বদল হওয়ার পরও অর্ধশতাধিক উদ্যোক্তার কারখানায় কোনো সমস্যা হয়নি। তাদেরও রাজনৈতিক পরিচয় সবার জানা। তারা আইন মেনে ব্যবসা করছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে নিয়ম মেনে। এ কারণে ব্যাংকের সঙ্গে তাদেরও কোনো সমস্যা হয়নি। কিছু কিছু অঘটন ঘটেছে, যা পুরো খাতের জন্য একটি নেতিবাচক বার্তা দিয়েছে, বায়াররা এখন পুরো বিষয়টা জানতে পারছে।
৩.
অর্থায়ন সমস্যার পরে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে, তা হল বন্দরের সক্ষমতার ঘাটতি। প্রতিবছর রপ্তানির আকার বাড়ছে, কিন্তু বন্দরসংশ্লিষ্ট সেবাগুলোর মান বাড়ছে না। লিড টাইম ধরে রাখতে উড়োজাহাজে পণ্য যাচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যে একটি ডেডিকেটেড সড়ক দরকার। রেল ও নদীপথে পণ্য পরিবহন বাড়াতে হবে। কিছু পণ্য আছে, যা দেরিতে পৌঁছালেও সমস্যা হয় না। সেগুলো যদি নদীপথে যায়, তাহলে সড়কের চাপ কমে যাবে। এতে রপ্তানি পণ্য পরিবহনে সড়কে বেশি চাপ থাকবে না। এটিও দরকার। বন্দর উন্নয়নের যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তা স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত করা উচিত শিল্পের স্বার্থে।
পোশাকশিল্পের অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক সংকটও মোকাবিলা করতে হয় বহুমুখী তৎপরতার মাধ্যমে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক এখন বড় ইস্যু। সরকার চেষ্টা করেছে শুল্কহার কমিয়ে আনতে। আরও কমতে পারে, না-ও পারে। শিল্পের জন্য স্বস্তিদায়ক হল, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পণ্যের ওপর শুল্কহার কম। এই সুবিধা আরও বড় পরিসরে নিতে হলে আমাদের জ্বালানির বিষয়টি সুরাহা করতে হবে। তখন বিদেশি বিনিয়োগও এ খাতে বেশি করে আসবে।
পোশাক খাতের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু, মানে এসএমভি-ভিত্তিক ফ্লোর প্রাইসিং চালু করতে পারলে বাংলাদেশে পুরো খাতটি একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে। দীর্ঘমেয়াদি টেকসইয়ের জন্য ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অনেক দেশে তা আছে। আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি; কারণ, চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন। উদ্যোক্তারাও একমত হতে সময় নিচ্ছেন। এটি হলে সঠিক সময় এবং পরিচালন ব্যয়ের ভিত্তিতে পণ্যের দাম নিশ্চিত করা যাবে। এর বাস্তবায়নে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের সঙ্গে ঐকমত্য জরুরি। সরকারও সে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। বিজিএমইএ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি কতটা বেড়ে যাবে, সেই বিশ্লেষণও দেওয়া যাবে।কাপড়ের সেরা দোকান
৪.
সব সময় উৎপাদনে থাকা পোশাক খাতে বিনিয়োগও কম নয়। এ জন্য প্রতিনিয়ত অর্থের চাহিদা থাকে, যা পুরোটাই ব্যাংক জোগান দেয়। পোশাক খাতের হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত। বলা যায়, পুরো খাত এখনো পুঁজিবাজারে আসেনি। এর জন্য পুঁজিবাজার কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে; উত্তরটা তাদের কাছেই। চার হাজারের বেশি পোশাক কারখানার মধ্যে ২৬৮টি লিড সার্টিফাইড। রপ্তানির স্বার্থে যদি আন্তর্জাতিক শর্ত মানা যায়, তাহলে কমপ্লায়েন্সের জন্য পুঁজিবাজারের শর্ত মানতে তো বাধা হতে পারে না। এখন যদি আবেদন শেষে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়, তাহলে তো কেউ যাবে না। তালিকাভুক্ত হতে পারবে কি পারবে না, তার নিষ্পত্তি দ্রুত করতে হবে। তালিকাভুক্ত প্রক্রিয়াটিও দ্রুত ঠিক করতে হবে। উদ্যোক্তাদের কাছে যেতে হবে। যে যার মত অর্থায়ন সংগ্রহ করছে। যেটা সহজ ও দ্রুত হয়, সেখানেই উদ্যোক্তারা যাবেন—এটাই স্বাভাবিক।